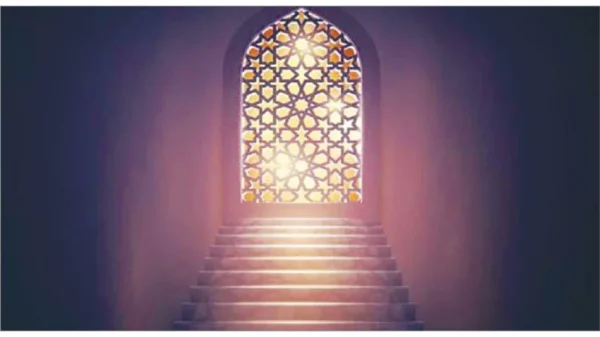মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৪৭ অপরাহ্ন
তথ্যের নিরাপত্তা বনাম নিরাপত্তা আইন

রাজেকুজ্জামান রতন:
মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে, তত তার জানার পরিধি বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে মানুষের সঙ্গে সংযোগ। আজ থেকে দুশত বছর আগে একজন মানুষ গড়ে কতজন মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকতেন, আর এখন কত মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকতে হয় তার একটা তুলনামূলক বিচার করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেমন বাড়ছে, তেমনি বিরোধটাও নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে। ফলে সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, সম্পর্কের মর্যাদা ও গোপনীয়তার ধারণা আজ আর আগের মতো নেই। বাবা-মা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী, সন্তানদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেমন আলাদা, তেমনি একজনের অ্যাকাউন্ট অন্যজনের পক্ষে ব্যবহার করা শুধু অসম্ভব নয়, কখনো কখনো অনুচিত। আবার খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাজার, চাকরি, যাতায়াত, বিনোদন, ব্যাংক কত বিষয়ে যে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়, তা গুনে শেষ করা যাবে না। ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেমন মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে, তেমনি তাদের মধ্যে একটা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে দিন দিন।
একজনের সঙ্গে অন্যজনের দেখা হলেই সাধারণ প্রশ্ন, কেমন আছ? সবাই সবার খবর জানতে চায়, খবর রাখতে চায়। কিন্তু এই জানার সীমা কতটুকু? তথ্য জানার অধিকার সবারই আছে। সঙ্গে সঙ্গে এই বিবেচনা থাকতে হবে যে, কোন বিষয়ের তথ্য, কে জানবে, কতটুকু জানতে পারবে আর ব্যক্তিগত তথ্য নিজে থেকে কেউ না দিলে তা গোপনে কেউ জানতে পারবে কিনা? কারও ঘরে উঁকি দিয়ে দেখা খুবই অশোভন একটি বিষয়, তেমনি কারও ব্যক্তিগত চিঠি, ডায়েরি তার অজ্ঞাতে পড়াটাও অন্যায় বলে বিবেচিত। ব্যক্তির পরিচয়পত্র কথাটির সঙ্গে পরিচয় থাকলেও জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার খুব বেশি দিন আগের নয়। প্রথমে নির্বাচনের জন্য শুরু হলেও, পরিচয়পত্র একজন ব্যক্তির শুধু ভোটের জন্য নয়, নানা ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়। ১৮ কিংবা তার বেশি বয়সী নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া হয়। এ ছাড়া এখন শিশুদের জন্মনিবন্ধন করাতে হয়। গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পাওয়া, পাসপোর্ট করা, জমি বেচাকেনা, মোবাইল ফোনের সিম কেনা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলাসহ ৩৮ ধরনের সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র দেখাতে হয়। এর বাইরে ব্যবসা নিবন্ধন, কর শনাক্তকরণ নম্বরসহ (টিআইএন) বিভিন্ন কাজে সরকারি সংস্থাকে ব্যক্তিগত তথ্য দেয় মানুষ। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন কাজে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু সেই তথ্য যদি সুরক্ষিত না থাকে, ফাঁস অথবা বেহাত হয়ে যায় তাহলে তো উদ্বিগ্ন হওয়ারই কথা।
২০০৭ সালে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছিল নির্বাচন কমিশন। সে সময় ভোটারদের জাতীয় পরিচয়পত্রও (এনআইডি) দেওয়া হয়। এখন ভোটারের নাম, মা-বাবার নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ছবিসহ কমবেশি ৩০ ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ভোটারের আঙুলের ছাপ ও চোখের মণির ছাপ (আইরিশ), ডিজিটাল স্বাক্ষর নেওয়া হয়। এসব সংগৃহীত তথ্য ইসির এনআইডি সার্ভারে সংরক্ষিত আছে। এনআইডির তথ্যভান্ডারে প্রায় ১২ কোটি ভোটারের কমবেশি ৩০ ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য আছে। ১৭১টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য যাচাই করার ক্ষেত্রে ইসির এই তথ্যভান্ডার থেকে তথ্য যাচাই-সংক্রান্ত সেবা নিয়ে থাকে। তথ্য এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষের এবং সমাজের জীবনে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যভান্ডারের কোনো ডিজাস্টার রিকভারি সাইট (ডিআরএস) বা যথাযথ ব্যাকআপ (বিকল্প সংরক্ষণব্যবস্থা) নেই। ডিআরএস না থাকায় জাতীয় এই তথ্যভান্ডার অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে থাকাটা স্বাভাবিক। ডিআরএস না থাকায় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে যদি এনআইডির তথ্যভান্ডার নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বিপুলসংখ্যক মানুষের তথ্য হারিয়ে যাওয়া এবং আর ফিরে না পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অনেক দিন ধরে এই বিকল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালুর (ব্যাকআপ) কথাবার্তা চললেও এখনো তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। এখন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) তথ্যের ব্যাকআপ রাখা হয়, কিন্তু তা যথাযথ নয় এবং যথেষ্টও নয়। সম্প্রতি উদ্বেগজনক একটি খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে এই সেবা নেয় এমন একটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে লাখ লাখ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়েছে। গত ৪ জুন ইসির জাতীয় পরিচয়পত্র, ভোটার তালিকা ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ কমিটির একটি সভা হয়। ওই সভায় জাতীয় তথ্যভান্ডারের ঝুঁকির বিষয়টি তুলে ধরেন ইসির আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং অ্যাকসেস টু সার্ভিসেস (আইডিইএ) প্রকল্পের (দ্বিতীয় পর্যায়) পরিচালক। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের কাজ করা হয়। এই বৈঠকে উল্লেখ করা হয় যে, বিকল্প কোনো ডিআরএস না থাকায় জাতীয় তথ্যভান্ডার অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, কমিশন গাজীপুর ও যশোরে ব্যাকআপ সার্ভার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত এটি কার্যকর হয়নি। ১৪ বছর কি যথেষ্ট সময় নয়, নাকি প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ছিল না, নাকি বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি আমাদের দেশের কর্তাদের কাছে? ইতিমধ্যে বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের ঘটনার খবর জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক অনলাইন সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চ। ৭ জুলাই তাদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে তথ্য ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে সরকারি একটি সংস্থার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। টেকক্রাঞ্চ আরও দাবি করেছে, তারা তথ্য ফাঁসের বিষয়ে জানতে বাংলাদেশের বিজিডি ই-গভ সার্ট, সরকারের প্রেস অফিস, ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং নিউ ইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশি কনস্যুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু কোনো সাড়া পায়নি। তথ্য ফাঁসের ঘটনা এটাই প্রথম নয়, বিজিডি ই-গভ সার্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৪ সালে হ্যাকাররা রাষ্ট্রমালিকানাধীন সোনালী ব্যাংকের নিরাপত্তাব্যবস্থা হ্যাক করলে আড়াই লাখ ডলার দিয়ে তবেই উদ্ধার পেতে হয়েছিল। সেই অর্থ তুরস্কের একটা হিসাবে পাঠাতে হয়েছিল। তবে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সাইবার আক্রমণ ছিল ২০১৬ সালে, বাংলাদেশ ব্যাংকে। অর্থ লেনদেনের সুইফট ব্যবস্থা হ্যাক করে ৮১০ কোটি ডলার চুরি করা হয়েছিল। সেই অর্থ চলে গিয়েছিল ফিলিপাইনে। আবার ২০১৯ সালে তিনটি স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংক বড় ধরনের সাইবার হামলার মুখে পড়েছিল। সে সময় ক্লোন ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে রাশিয়া, ইউক্রেন ও সাইপ্রাস থেকে তিন ব্যাংকের ক্যাশ মেশিন থেকে ৩০ লাখ ডলার চুরি করা হয়। আবার বিজিডি ই-গভ সার্ট ডার্কওয়েবে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকের ৩ হাজার ৬৩৯টি ক্রেডিট কার্ড খুঁজে পেয়েছিল। এসব কার্ড ব্যবহার করে ৪ কোটি ৩৬ লাখ ৬৮ হাজার ডলার তুলে নেওয়ার ঝুঁকির মধ্যে ছিল ব্যাংকগুলো। এই ঝুঁকি কেবল ব্যাংকেরই ছিল না, কার্ডের মালিক যারা তারাও ঝুঁকির মধ্যে ছিলেন। কিন্তু কেন এবং কীভাবে এসব ঘটনা ঘটেছিল এবং এ ঘটনায় কারা যুক্ত ছিল, তাদের কারও শাস্তি হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।
জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন বিভাগের সার্ভারে (তথ্যভান্ডার) জালিয়াতি করে অবৈধ পরিচয়পত্র তৈরি, করোনাকালে বাংলাদেশের মানুষকে টিকা দিতে সুরক্ষা নামে যে ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছিল, সেখানেও জালিয়াতি করে সনদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সরকারি মহল থেকে বারবার বলা হয়ে থেকে যে, ডিজিটাল জগতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে এনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করেছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই আইনকে ব্যবহার করে মানুষের নিরাপত্তার বদলে সংবাদমাধ্যম ও বিরোধী কণ্ঠ রোধেই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন আবার উপাত্ত সুরক্ষা আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলছে। এই আইনের খসড়া নিয়েও বিভিন্ন মহলের বিশেষজ্ঞ যারা অংশীজন হিসেবে বিবেচিত তাদের আপত্তি রয়েছে। তাদের আশঙ্কা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো এই আইনও কণ্ঠ রোধে ব্যবহার করা হবে যা নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন উঠছে।
লেখক: রাজনৈতিক সংগঠক ও কলামিস্ট
সূত্র: দেশরূপান্তর/ভয়েস/আআ